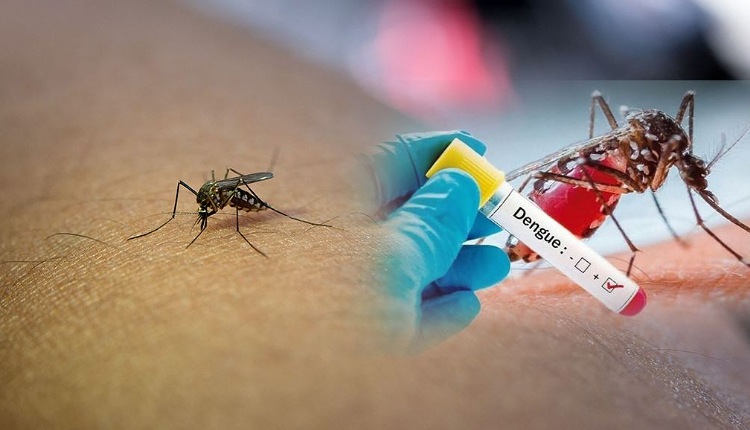শিক্ষা সংস্কারে শিক্ষকের ভাবনা

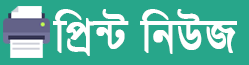
ডিআইইউ প্রতিনিধি: শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড—একথা আমরা প্রায়শই শুনে থাকি। কিন্তু এই মেরুদণ্ডকে সুসংহত করে রাখার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যাঁদের, তাঁরা হলেন শিক্ষকবৃন্দ।
একজন যোগ্য শিক্ষক কেবল পাঠ্যবইয়ের পাঠদানেই সীমাবদ্ধ থাকেন না; বরং তার বাইরে গিয়ে শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানসিক বিকাশের পথপ্রদর্শক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন।
আমাদের সমাজে শিক্ষকতা পেশাকে একসময় “মহান পেশা” হিসেবে বিবেচনা করা হতো, কেননা শিক্ষকই একটি প্রজন্মকে গড়ে তোলার মূল কারিগর। আজকের তথ্যপ্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষকতার ভূমিকা আরও ব্যাপকতা পেয়েছে।
শিক্ষক শব্দটি উচ্চারণ করলেই আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে একজন জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও দায়িত্ববান ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি।
তবে শিক্ষকতা শুধু পেশা নয়; এটি এক ধরনের সাধনা। কারণ, একজন প্রকৃত শিক্ষককে কেবল শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করলেই চলে না, তাঁকে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশে সহযোগিতা করতে হয়।
এর মধ্যে পড়ে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদার সাথে শিক্ষার্থীদের মানিয়ে নেওয়ার উপায় শেখানো, এমনকি জীবনের নানা চড়াই-উতরাই পেরোতে মানসিক শক্তি জোগানো।
শিক্ষকদের কাজ বহুমুখী। তাঁরা পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করে তোলেন এবং শিক্ষার্থীদের মনে শেখার আগ্রহ জাগিয়ে তোলেন।
আবার একই সঙ্গে একজন আদর্শ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা, সততা, দায়িত্ববোধ এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বীজ বপন করেন। কোনো একক সূত্রে সব ধরনের শিক্ষার্থীকে শেখানো সম্ভব নয়।
তাই শিক্ষককে প্রতিনিয়ত নতুন পদ্ধতি ও পঠনপাঠনের কৌশল খুঁজে বের করতে হয়। যেমন—নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার, কর্মমুখী শিক্ষা, প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষা ইত্যাদি।
অন্যদিকে, শিক্ষা শুধু কাগুজে সার্টিফিকেট অর্জনের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ নয়। শেখার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিত্ব গঠন ও জীবন দক্ষতা অর্জন করা।
একজন শিক্ষককে এ বিষয়েও নজর দিতে হয় যে, শিক্ষার্থীরা যেন সৃজনশীলভাবে চিন্তা করতে শেখে, সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবনী পথ খুঁজে পায়, এবং মানবিক মূল্যবোধের সাথে বেড়ে ওঠে।
সুতরাং, একজন আদর্শ শিক্ষকের প্রধান লক্ষ্য হল ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং নৈতিক—তিনটি ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর বিকাশ নিশ্চিত করা।
আজকের শিক্ষার্থীরা আগের তুলনায় অনেক বেশি প্রযুক্তিনির্ভর। ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, স্মার্ট ডিভাইস—এগুলো সবই এখন শিক্ষার্থীদের হাতের মুঠোয়।
ফলে তাঁরা দ্রুত তথ্য খুঁজে পেতে পারে, বহুমুখী জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়। তাই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক আগের চেয়ে আরও গতিশীল ও দ্বিমুখী হওয়া প্রয়োজন।
একসময় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের কথা একতরফাভাবে শোনাই ছিল মুখ্য। কিন্তু এখন শিক্ষার্থীরা চায় এমন শিক্ষক, যিনি তাঁদের প্রশ্ন, মতামত ও কৌতূহলকে স্বাগত জানাবেন।
শিক্ষার্থীরা এমন শিক্ষককে পছন্দ করে, যিনি বন্ধুসম আচরণ করেন। একজন সুন্দর মন-মানসিকতার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়টিও মজা করে শেখাতে পারেন।
ক্লাসে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব শিক্ষার গুণগত মানকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়।
অনেক সময় দেখা যায়, কঠিন গণিতের সূত্র বা ভাষা শেখার জটিলতা—একটু ব্যতিক্রমী উদাহরণ বা গল্পের মাধ্যমে সহজ হয়ে যায়। সেই দক্ষতা শিক্ষকেরই দেখাতে হয়।
এছাড়া, শিক্ষার্থীরা চায়, শিক্ষক হোন একজন পরামর্শদাতা (মেন্টর)। কারণ, কৈশোর ও তারুণ্যে তারা নানা মানসিক চাপে থাকে—পড়াশোনা, ক্যারিয়ার, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, এমনকি পারিবারিক চাপে দিকভ্রান্ত হতে পারে।
এই সময়ে যদি একজন শিক্ষক সঠিক দিকনির্দেশনা দেন, উৎসাহ দেন, নিরুৎসাহিত হওয়া শিক্ষার্থীও নতুনভাবে উদ্দীপ্ত হতে পারে।
তাছাড়া, “মন্দকে শুধরে ভালো গড়ে তোলা”—এটাই শিক্ষকের বড় গুণ। শিক্ষার্থীরা তাই সবসময় শাসনের চেয়েও স্নেহ ও সহমর্মিতা আশা করে।
শিক্ষককে আমাদের সমাজে বরাবরই সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয়। “শিক্ষক” শব্দটি উচ্চারণে যে আভিজাত্য ও গাম্ভীর্য ফুটে ওঠে, সেটি আমাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিরই অংশ।
প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, “গুরু-শিষ্য” সম্পর্ক ছিল শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার মূল ভিত্তি। সেই পরম্পরায় শিক্ষককে কেবল জ্ঞানের উৎস মনে করা হতো না, বরং তিনি ছিলেন নীতিনৈতিকতার মূর্ত প্রতীক।
তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিদায়ের দিন শিক্ষার্থীরা অশ্রুসিক্ত হয়ে প্রিয় শিক্ষকের কাছে বিদায় নিত।
তবে, সময় বদলেছে। আজকাল কিছু শিক্ষক কোচিং বাণিজ্য বা ব্যক্তিগত স্বার্থে কাজ করে সমালোচিত হন। এটাও আমাদের সমাজের বাস্তবতা।
কিন্তু এখনো বিপুলসংখ্যক শিক্ষক নিঃস্বার্থ ভাবে ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যতের কথা ভেবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁদের আন্তরিকতা, দায়িত্ববোধ ও মমত্ববোধ শিক্ষার্থীদের মনকে আলোকিত করে।
শুধু পাঠদান নয়, আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল পরিবারের সন্তানদের জন্য বৃত্তির বন্দোবস্ত করা বা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানো—এ সবকিছুই একজন যোগ্য শিক্ষক করে থাকেন।
এইসব উদাহরণই প্রমাণ করে শিক্ষকতা কেবলমাত্র পেশা নয়, বরং মানবসেবার এক বিশাল ক্ষেত্র।
একজন শিক্ষককে সম্মান জানাতে শুধু ফলের তোড়া বা সংবর্ধনাই যথেষ্ট নয়। প্রকৃত সম্মান হল তাঁর আদর্শ ও নৈতিক শিক্ষাকে জীবনে ধারণ করা।
যেসব শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে সমাজে নেতৃত্ব দেবে, নীতিনৈতিকতার পথ ধরে নতুন উদ্ভাবন করবে, তারাই প্রকৃত অর্থে শিক্ষকের মুখ উজ্জ্বল করে।
আবার শিক্ষকও তাঁর শিক্ষার্থীর সাফল্যে গর্বিত হয়ে বলেন, “ওই ছেলেটা বা ওই মেয়েটা আমার হাতে গড়ে উঠেছে।” এই পারস্পরিক বন্ধনই হল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ভালোবাসার গভীরতা।
শিক্ষকদের মর্যাদা রক্ষায় সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোও গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চশিক্ষাসহ সব স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণ, সম্মানজনক বেতন-ভাতা, গবেষণার সুযোগ ইত্যাদি থাকতে হবে।
একবার একজন শিক্ষক সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পেলে তিনি তাঁর সমস্ত মনোযোগ শিক্ষার্থীদের উন্নয়নে ব্যয় করতে পারেন। আর তখনই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেরা গুণাবলির বিকাশ ঘটে।
তাছাড়া, সাধারণ মানুষ এবং পরিবারগুলোও শিক্ষকদের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখাবে, যদি তারা দেখতে পায় শিক্ষকরা নিষ্ঠার সাথে তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন।
সার্বিকভাবে দেখা যায়, একজন শিক্ষকের ভূমিকা অনেক বিস্তৃত এবং সম্মানজনক। আমাদের সমাজে শিক্ষকদের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা এত দিন ধরে যে উচ্চতায় পৌঁছেছে, তার পেছনে আছে তাঁদের ত্যাগ, মমত্ব এবং সমাজ গড়ার ব্রত।
আবার, বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা চায় এমন শিক্ষক, যিনি আধুনিক প্রেক্ষাপটে তাদের কৌতূহল ও চাহিদা মেটাতে পারবেন।
প্রযুক্তি-সক্ষমতা, উদ্ভাবনী চিন্তা ও মেধাকে বিকশিত করতে পারা, আর নৈতিকতার আলো দেখাতে পারা—এই সবকিছু মিলিয়ে একজন শিক্ষককে হতে হয় “সবগুণের মানব।”
আমরা যদি সত্যিকার অর্থে সমৃদ্ধ জাতি গড়তে চাই, তবে শিক্ষার মানোন্নয়নই হবে মূল চাবিকাঠি। আর সেই শিক্ষার মানোন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন শিক্ষকবৃন্দ।
তাঁরা যথাযথ মর্যাদা, ভালোবাসা ও সহযোগিতা পেলে শিক্ষার্থীরা আরও বেশি উদ্দীপ্ত হবে। নতুন প্রজন্ম পাবে সঠিক দিকনির্দেশনা, সুস্থ মানসিক বিকাশ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি।
আর এই নতুন প্রজন্মের হাত ধরেই গড়ে উঠবে আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক, সংস্কৃতিমনা ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ। একজন আদর্শ শিক্ষকের ভূমিকা তাই কেবল শ্রেণিকক্ষের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা যায় বহুদূর, আমাদের সামগ্রিক সামাজিক ও জাতীয় বিকাশের চালিকাশক্তি হিসেবে।
মিলি রহমান
সহযোগী অধ্যাপক
ইংরেজি বিভাগ এবং
জয়েন্ট ডিরেক্টর রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন সেল
ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি